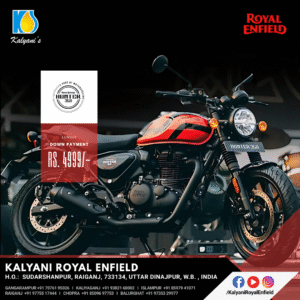Last Updated on [modified_date_only] by Shroddha Bhattacharyya
ইন্ডিয়া টুডে ফ্যাক্ট চেক: মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা পবিত্র রমজান মাসে (Fact Check) তারাবির নমাজ পড়ে থাকেন। আর এই নমাজকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। এই ভিডিওতে এক মুসলিম বৃদ্ধকে সেনার পোশাকে থাকা কয়েকজন ব্যক্তিকে মারধর ও অত্যাচার করতে দেখা যাচ্ছে।
ভিডিওটি পোস্ট করে দাবি করা হচ্ছে যে এটি নয়াদিল্লির ঘটনা (Fact Check) এবং তারাবির নমাজ পড়ার কারণে ওই বৃদ্ধকে এমনভাবে মারধর করা হয়েছে।

আজতক ফ্যাক্ট চেক অনুসন্ধান করে দেখেছে যে (Fact Check) ভিডিওটি প্রায় ১৬ বছর আগেকার এবং ভারতের নয় বরং পাকিস্তানের একটি ঘটনা। এর আগেও মিথ্যে দাবিতে ভিডিওটি শেয়ার হয়েছে।
যেভাবে জানা গেল সত্যি (Fact Check)
ভাইরাল ভিডিওটি থেকে স্ক্রিনশট সংগ্রহ করে তার রিভার্স ইমেজ সার্চ (Fact Check) করা হলে ওই একই ক্লিপের বর্ধিত প্রায় ১০ মিনিটের একটি সংস্করণ Dailymotion নামক ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় যা আজ থেকে ১৬ বছর আগে পোস্ট করা হয়েছিল। এর থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার হয় যে ভিডিওটি এখনকার নয়, বরং অন্তত ১৬ বছর আগের।

সেই সঙ্গে ভিডিওটি পোস্ট করে লেখা হয় যে এখানে পাকিস্তানি আর্মিকে (Fact Check) একজন মুসলিম বৃদ্ধকে মারধর করতে দেখা যাচ্ছে। এর থেকে আন্দাজ করা যায় যে ভিডিওটি পাকিস্তানের হতে পারে।
আরও পড়ুন: Fact Check: বাংলাদেশে আগুনের পাশে গাছে বেঁধে রাখা এই যুবক হিন্দু নয়, মুসলিম
এই সূত্র কাজে লাগিয়ে কিছু কিওয়ার্ডের সাহায্যে (Fact Check) সার্চ করা হলে ওই একই ভিডিও-র স্ক্রিনশট ব্যবহার করে আল জাজিরার একটি খবর দেখতে পাওয়া যায় যা ২০০৯ সালের ২ অক্টোবর প্রকাশ করা হয়েছিল। এই খবরে লেখা হয়, তালিবানের সঙ্গে যোগসূত্র রয়েছে এই সন্দেহে ভিডিওতে থাকা ওই ব্যক্তিদের মারধর করে পাক সেনাবাহিনী। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে পাল্টা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়।

প্রতিবেদনে তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মুখপাত্র মেজর জেনারেল আতহার আব্বাসের একটি বিবৃতিও রয়েছে, যিনি বলেছিলেন, সেনাবাহিনী অভিযোগের প্রেক্ষিতে এই নির্যাতনের তদন্ত করছে। তবে, প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে ভিডিওটি কোথায় বা কখন ধারণ করা হয়েছিল এবং এটি কতটা সত্য তা স্পষ্ট নয়।
ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের একটি খবরেও এই ঘটনা এবং ভিডিও-র কথা তুলে ধরা হয়। সঙ্গে লেখা হয়, যে ভিডিওটি সম্ভবত সোয়াত উপত্যকায় তোলা হয়েছে। এর পাশাপাশি ঘটনাটি নিয়ে বিবিসি-ও একটি খবর ২০০৯ সালের ১ অক্টোবর প্রকাশ করেছিল। সেখানেও লেখা হয়েছে যে ঘটনাটি সম্ভবত সোয়াত ভ্যালির।
প্রসঙ্গত, এর আগে ২০১৯ সালেও এই ভিডিওটি ভারতের কাশ্মীরের ঘটনা বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা হয়েছিল। তখন ইন্ডিয়া টুডের পাশাপাশি দ্য কুইন্টের মতো ফ্যাক্ট চেকিং সংস্থার পক্ষ থেকেও এই নিয়ে খবর করা হয়।
ফলে বোঝাই যাচ্ছে যে পাকিস্তানের একটি ১৬ বছর আগেকার ঘটনাকে বর্তমানে ভারতের বলে মিথ্যে দাবি ছড়ানো হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।
এই খবরটি শক্তি কালেক্টিভের অংশ হিসাবে প্রথমে ইন্ডিয়া টুডে দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল, পরবর্তীতে ট্রাইব টিভি বাংলার দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। এই খবরটির হেডলাইন ও সারসংক্ষেপ বাদে বাকি খবর ট্রাইব টিভি বাংলার কর্মীরা সম্পাদনা করেনি।