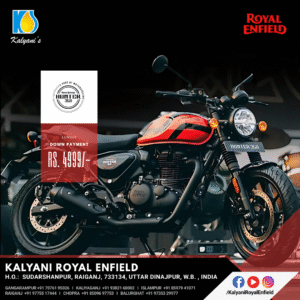Last Updated on [modified_date_only] by Aditi Singha
ট্রাইব টিভি বাংলা ডিজিটাল: আপনার কাছে নেটপাড়া কী (Language)? শুধুই কি বিনোদনের অংশ বিশেষ! বড্ড ভুল না হলে, নেট দুনিয়ায় ক্রমাত ছুটে চলেছে ‘বিনোদন’। কখনো ধ্বংস করছে আবার কখনো নতুনের পথ দেখাচ্ছে। নেটপাড়া কে হাতিয়ার করে, পুরোনো ছন্দে নতুনের গান করাই যায়? দেখা যাক, বলার ভাষা ও লেখার ভাষা কোথায় আলাদা?
বাংলা ভাষা এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের ধারক (Language)। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর ব্যবহারিক রূপ—কথ্য ভাষা ও লেখ্য ভাষা—দুই ভিন্ন ধারায় গড়ে উঠেছে। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তাকে কথ্য ভাষা বলা হয়। আর সাহিত্য, প্রবন্ধ, সংবাদপত্র বা সরকারি নথিপত্রে ব্যবহৃত পরিশীলিত রূপকে বলা হয় লেখ্য ভাষা।

কথ্য ভাষা (Language)
কথ্য ভাষা সহজ-সরল ও প্রাণবন্ত। মানুষের আবেগ, দৈনন্দিন অভ্যাস, আঞ্চলিক উচ্চারণ—সবকিছু এতে জায়গা করে নেয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা বিভূতিভূষণের উপন্যাসে চরিত্রদের সংলাপে এই কথ্যতার ছাপ স্পষ্ট। যেমন, “তুই কোথায় যাচ্ছিস?”, “কি খবর?”, “চল যাই”—এসব বাক্য সাধারণের মুখের ভাষার প্রতিফলন।
লেখ্য ভাষা (Language)
লেখ্য ভাষা তুলনামূলকভাবে মার্জিত ও ব্যাকরণসম্মত। এটি প্রধানত সংস্কৃতনির্ভর এবং দীর্ঘ বাক্য নির্মাণে সমৃদ্ধ। প্রবন্ধ, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন বা উচ্চাঙ্গ সাহিত্যে লেখ্য ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ:
“আজকের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেশজুড়ে এক নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।”
এখানে কথ্য ভঙ্গি নেই, বরং একটি গম্ভীর ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লক্ষ্য করা যায়।
বিদেশি শব্দের প্রবেশ কথ্য বাংলায়! (Language)
বাংলা কথ্য ভাষার বৈশিষ্ট্য হলো এর সহজাত গ্রহণক্ষমতা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাণিজ্য, আক্রমণ, উপনিবেশ এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ফলে বাংলায় বহু বিদেশি শব্দ ঢুকে পড়েছে। এসব শব্দ এতটাই দৈনন্দিন ব্যবহারে মিশে গেছে যে আজ সেগুলো ছাড়া আমাদের কথা অসম্পূর্ণ মনে হয়।
আরবি-ফারসি উৎসের শব্দ (Language)
মুসলিম শাসনামলে বাংলা ভাষায় বিপুল আরবি-ফারসি শব্দ প্রবেশ করে।
দুনিয়া, হাওয়া, খবর, হিসাব, দফতর, কিতাব, বাজার, জামা, বখত, দাওয়াত ইত্যাদি আজও ব্যবহৃত হয়।
এগুলো প্রধানত কথ্য বাংলায় সহজে মিশে গিয়ে সাধারণ মানুষের ভাষার অংশ হয়ে গেছে।
পর্তুগিজ উৎসের শব্দ (Language)
ষোড়শ শতকে বাংলায় আসা পর্তুগিজ ব্যবসায়ীরা অনেক নতুন শব্দ রেখে গেছেন।
আলমারি, জানালা, পাউরুটি, চাবি, তোয়ালে, বন্দর প্রভৃতি কথায় পর্তুগিজ প্রভাব আজও টিকে আছে।
ইংরেজি উৎসের শব্দ (Language)
ব্রিটিশ শাসনের ফলে ইংরেজি ভাষার প্রভাব সর্বাধিক।
টেবিল, চেয়ার, অফিস, স্কুল, হাসপাতাল, ডাক্তার, ট্রেন, বাস, লরি, পোস্ট, ব্যাংক ইত্যাদি শব্দ প্রতিদিনের কথাবার্তায় ব্যবহার করি।
আধুনিক যুগে কম্পিউটার, মোবাইল, ইন্টারনেট, অনলাইন, ফাইল, ড্রাইভ প্রভৃতি ইংরেজি শব্দও অবলীলায় ব্যবহৃত হয়।
হিন্দি ও উর্দুর প্রভাব
চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ফলে হিন্দি-উর্দুর বহু শব্দ কথ্য বাংলায় ঢুকে গেছে।
যেমন: মজা, দোস্ত, ঝামেলা, ফাটাফাটি, বেলুন, দিদি, ভাইয়া ইত্যাদি।
অন্যান্য ভাষার প্রভাব
তামিল, তেলেগু, মারাঠি, এমনকি চীনা উৎস থেকেও কিছু শব্দ বাংলায় এসেছে। যেমন চা (চীনা), লরি (মারাঠি উৎস), আনাজ (হিন্দি উৎস) ইত্যাদি।
বাংলা কথ্য ও লেখ্য ভাষার ভিন্নতা যেমন সাহিত্যকে বৈচিত্র্যময় করেছে, তেমনই বিদেশি শব্দের প্রবেশ এটিকে করেছে আরও সমৃদ্ধ। লেখ্য ভাষা যেখানে গাম্ভীর্য ও শৃঙ্খলার প্রতীক, কথ্য ভাষা সেখানে প্রাণবন্ত, বহুজাতিক যোগাযোগের বাহক। এ দুই রূপের পারস্পরিক সম্পর্কই বাংলা সাহিত্যের আসল শক্তি।